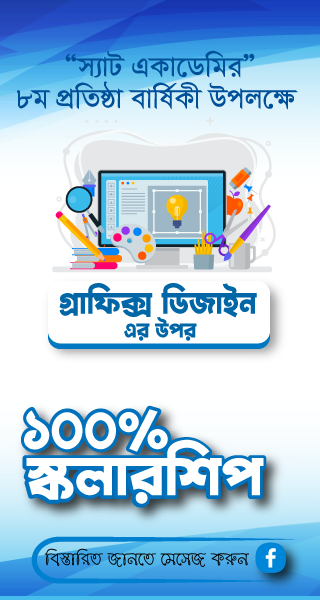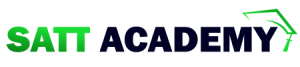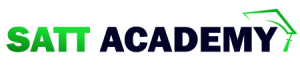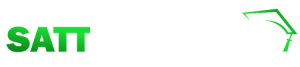মহান স্রষ্টার পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন রকমের পদার্থ। কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, আর কোনটি বা বায়বীয় । প্রতিটি পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে ক্ষুদ্র কণা আকারে আনা যায়। এরূপ অতি ক্ষুদ্র কণা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে সে পদার্থের গুণ বিদ্যমান থাকে, তাকে সে পদার্থের অনু (Molecule) বলে। অনুকে ভাঙলে পাওয়া যায় পরমাণু কিন্তু পরমাণুকে ভাঙলে কী পাওয়া যাবে? হ্যাঁ পরমাণুকে ভাঙলে দুইটি জিনিস পাওয়া যাবে।
(১) নউক্লিয়াস (Nucleus)
(২) ইলেকট্রোন (Electron)
নিউক্লিয়াস পরমাণুর মধ্যস্থলে থাকে এর মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটনের আছে ধনাত্মক চার্জ, আর নিউট্রনের কোন চার্জ নাই। ইলেকট্রোন অতি হালকা কণিকা। এরা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। এদের ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় ১৮৩৭ ভাগ মাত্র। প্রত্যেকটি পরমাণুতে যতটি ধনাত্বক চার্জের প্রোটন থাকে ঠিক ততটি ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রোন থাকে। ফলে পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় (Neutral) থাকে। যদি কোন হালকা একটি ইলেকট্রোন সরিয়ে অন্য পরমাণুতে আনা যায়, তখন যেখান হতে ইলেকট্রোন আসল তথায় হবে ধনাত্মক চার্জ এবং যেখানে ইলেকট্রোন যোগ হলো সেখানে হবে ঋণাত্বক চার্জ, আর এ ইলেকট্রোন এর প্রবাহকেই বলা হয় ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ। যার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় পরিবাহী।
কোন নির্দিষ্ট প্রস্থচ্ছেদের ইলেকট্রিক কারেন্ট দুই প্রকার
(১) একমুখী প্রবাহী বা ইংরেজিতে ডাইরেক্ট কারেন্ট (সংক্ষেপে একে ডিসি বলে
(২) পরিবর্তী প্রবাহী বা ইংরেজিতে অলটার নেটিং কারেন্ট (সংক্ষেপে একে এসি বলে)
(১) ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ডি.সি. পেতে সাধারণত ডি. সি. ডিজেল জেনারেটর বা ডি.সি. রেকটিফায়ার ব্যবহৃত হয়। ডি.সি. স্বাধারণত অধিক গুণাগুণ সম্পন্ন ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাতু এবং পুরত্ব ও গুণাগুণ সম্পন্ন ইলেকট্রোড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সে সব ক্ষেত্রে ডি.সি. কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে পোলারিটি পরিবর্তন করা যায়। সাধারণত ভারী ধাতু জোড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।
(২) যে সব ক্ষেত্রে পাতলা ধাতু জোড় দেওয়া হয়, সে সব ক্ষেত্রে এ.সি কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে পোলারিটি পরিবর্তন করা যায় না।
(ক) ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো বৈদ্যুতিক সংজ্ঞা
(১) ভোল্টেজ (Voltage )
(২) রেজিস্ট্যান্স (Resistance)
(৩) অলটারনেটিং কারেন্ট (এসি) (AC)
(৪) ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডিসি) (D.C)
(৫) ইলেকট্রিক পাওয়ার (Electric Power )
(৬) সার্কিট (Circuit)
(৭) পোলারিটি (Polarity)
(৮) স্ট্রেট পোলারিটি (Straight Polarity)
(৯) রিভার্স পোলারিটি (Reverse Polarity)
(১০) আর্ক ভোল্টেজ ( Arc Voltage)
(১১) ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Open Circuit Voltage)
(১২) স্ট্রাইকিং ভোল্টেজ (Striking Voltage)
(১৩) আর্ক বো (Are Blow)
(১৪) তার (Wire)
(১৫) ক্যাবল (Cable)
(খ) ওয়েল্ডিং এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সংজ্ঞাগুলোর বর্ণনাঃ
ভোল্টেজঃ নলের মধ্য দিয়ে পনি প্রবাহিত করতে যেমন চাপের প্রয়োজন অনুরূপভাবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করতে চাপের প্রয়োজন হয় এবং চাপকে ভোল্টেজ বলে। এর এককের নাম ভোল্ট ।
রেজিস্ট্যান্সঃ কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় উক্ত পদার্থ যে বাধা প্রদান করে তাকে ঐ পদার্থের রেজিস্ট্যান্স বলে। রেজিস্টান্স পরিমাপের এককের নাম ওহম।
অলটারনেটিং কারেন্ট (এসি) যে বিদ্যুৎ প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে তাকে পরিবর্তী প্রবাহ বা ইংরেজিতে অলটারনেটিং কারেন্ট বলে। (সংক্ষেপে এসি বলা হয়)
ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডিসি) যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় দিক পরিবর্তন করে না, তাকে একমুখী প্রবাহ বা ইংরেজিতে ডাইরেক্ট কারেন্ট বলে (সংক্ষেপে ডিসি বলে)।
ইলেকট্রিক পাওয়ার কোন সার্কিটে বলের সাহায্যে একক সময়ে যে কাজ হয় তাকে ইলেকট্রিক পাওয়ার বলে। এর একক ওয়াট। এক ওয়াটকে এক হাজার গুণ করলে তাকে কিলোওয়াট বলে। অর্থাৎ ১ ওয়াট x১০০০= ১ কিলোওয়াট।
সার্কিট ইলেকট্রিসিটি চলার পথকে বাংলায় বর্তনী এবং ইংরেজিতে সার্কিট বলে।
পোলারিটি কোন সার্কিটে ইলেট্রোন কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা নির্দেশ করাকে পোলারিটি বলে। উলেখ্য যেহেতু ডিসি একমুখী সুতরাং এর পোলারিটি আছে কিন্তু এসি প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে তাই এর কোন পোলারিটি নেই। ওয়েল্ডিং ক্ষেত্রে এ পোলারিটির গুরুত্ব অপরিসীম।
Promotion